WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-42
WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-42
ভূগোলিকা-Bhugolika -তে সবাইকে স্বাগত জানাই। এই পোস্টে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (WBSSC) -এর স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট (SLST) -এর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য প্রদত্ত ভূগোল (IX-X & XI-XII) -এর পাঠ্যসূচি অনুসারে পর্ব-৪২ -তে (WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-42) ৫০ টি MCQ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।
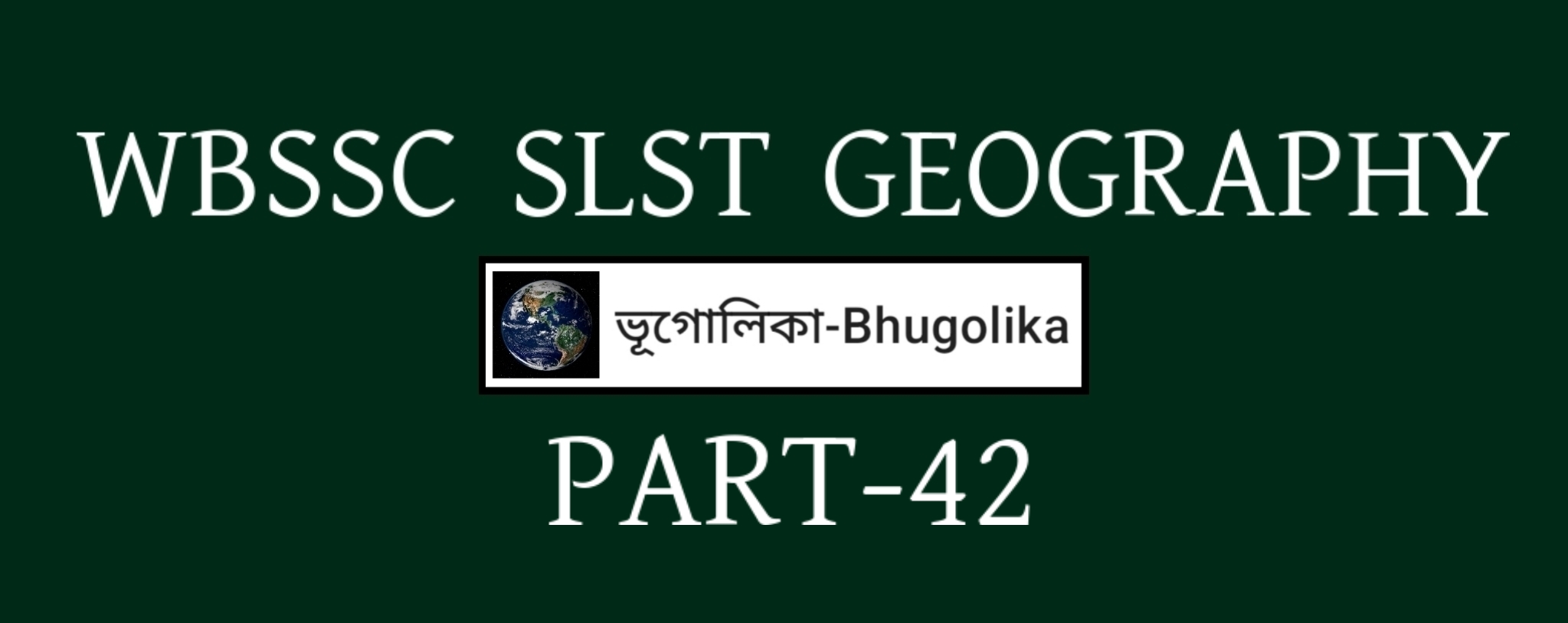
(২০৫১) ভূপৃষ্ঠের মাধ্যমে যে পদ্ধতিতে অধঃক্ষেপিত জল মৃত্তিকা বা শিলার ভেতরে প্রবেশ করে, তাকে বলে —
(A) অনুস্রাবণ (B) প্রস্বেদন
(C) বাষ্পীভবন (D) অধঃক্ষেপণ
উত্তর : (A) অনুস্রাবণ।
(২০৫২) জলবিদ্যাতে অনুস্রাবণ (Infiltration) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন —
(A) উইলিয়াম গ্লেন হইট (B) রবার্ট এলমার হর্টন
(C) উইলিয়াম মরিস ডেভিস (D) রবার্ট ফিলিপ শার্প
উত্তর : (B) রবার্ট এলমার হর্টন।
(২০৫৩) রবার্ট এলমার হর্টন (Robert Elmer Horton) যে সালে জলবিদ্যাতে অনুস্রাবণ (Infiltration) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন —
(A) ১৯৩৩ (B) ১৯৩৪
(C) ১৯৩৫ (D) ১৯৩৬
উত্তর : (A) ১৯৩৩।
(২০৫৪) যে মাটিতে অনুস্রাবণ হার সবচেয়ে বেশি —
(A) বেলে মাটি (B) দোয়াঁশ মাটি
(C) কাদা মাটি (D) লাল মাটি
উত্তর : (A) বেলে মাটি।
(২০৫৫) মৃত্তিকার বা শিলার রন্ধ্রের মধ্যে জলের প্রবেশকে বলে —
(A) পারকোলেশন (B) ট্রান্সমিশন
(C) ইনফিলট্রেশন (D) প্রেসিপিটেশন
উত্তর : (A) পারকোলেশন।
(২০৫৬) পারকোলেশন (Percolation) সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন —
(A) ব্রডবেন্ট ও হর্টন (B) ব্রডবেন্ট ও গিলবার্ট
(C) ব্রডবেন্ট ও হ্যামার্সলে (D) ব্রডবেন্ট ও হইট
উত্তর : (C) ব্রডবেন্ট ও হ্যামার্সলে।
(২০৫৭) ব্রডবেন্ট ও হ্যামার্সলে (Broadbent & Hammersley) যে সালে পারকোলেশন (Percolation) সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন —
(A) ১৯৫৪ (B) ১৯৫৫
(C) ১৯৫৬ (D) ১৯৫৭
উত্তর : (D) ১৯৫৭।
(২০৫৮) India-WRIS অনুসারে, ভারতে প্রধান নদী অববাহিকার সংখ্যা —
(A) ১২ টি (B) ১৫ টি
(C) ১৮ টি (D) ২১ টি
উত্তর : (A) ১২ টি
(২০৫৯) India-WRIS অনুসারে, ভারতে মাঝারি নদী অববাহিকার সংখ্যা —
(A) ৪২ টি (B) ৪৪ টি
(C) ৪৬ টি (D) ৪৮ টি
উত্তর : (C) ৪৬ টি।
(২০৬০) বিশ্বের বৃহত্তম নদী অববাহিকা হল —
(A) ইয়াংসি অববাহিকা (B) আমাজন অববাহিকা
(C) মিসিসিপি অববাহিকা (D) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা
উত্তর : (B) আমাজন অববাহিকা।
(২০৬১) ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকা হল —
(A) গঙ্গা অববাহিকা (B) গোদাবরী অববাহিকা
(C) কৃষ্ণা অববাহিকা (D) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা
উত্তর : (A) গঙ্গা অববাহিকা।
(২০৬২) ‘Rainfall-Runoff Modelling: The Primer’ (২০০১) গ্রন্থটি রচনা করেন —
(A) মাইকেল সেলবি (B) কার্ক ব্রায়ান
(C) ডেভিড লিনটন (D) কিথ বেভেন
উত্তর : (D) কিথ বেভেন।
(২০৬৩) বৃষ্টিপাতের ফোঁটার আকার ও গতিবেগ পরিমাপ করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে —
(A) পিজোমিটার (B) ডিসড্রোমিটার
(C) অ্যানিমোমিটার (D) হাইগ্রোমিটার
উত্তর : (B) ডিসড্রোমিটার।
(২০৬৪) ‘Replenish: The Virtuous Cycle of Water and Prosperity’ (২০১৭) গ্রন্থ রচনা করেন —
(A) কিথ বেভেন (B) সান্দ্রা পোস্টেল
(C) জন চেরি (D) আন্দ্রিয়া রিনাল্ডো
উত্তর : (B) সান্দ্রা পোস্টেল।
(২০৬৫) মহাসাগরের গড় জল বিনিময় সময় (Water Exchange Time) হল —
(A) ১০০০ বছর (B) ২০০০ বছর
(C) ৩০০০ বছর (D) ৫০০০ বছর
উত্তর : (C) ৩০০০ বছর।
ভূমিরূপবিদ্যা (Geomorphology) : ভূমিরূপ ও প্রক্রিয়া — নদীজাত, হৈমিক/হিমবাহজাত, বায়ুজাত, কার্স্ট এবং সামুদ্রিক (Landform and Process — Fluvial, Glacial, Wind, Karst and Marine) [IX-X & XI-XII]
ভূমিরূপ ও প্রক্রিয়া — নদীজাত
(২০৬৬) পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী (World’s Longest River) হল —
(A) আমাজন (B) নীল
(C) কঙ্গো (D) ব্রহ্মপুত্র
উত্তর : (B) নীল।
(২০৬৭) জলপ্রবাহ অনুসারে, পৃথিবীর বৃহত্তম নদী (World’s Largest River) হল —
(A) ব্রহ্মপুত্র (B) ইয়াংসি
(C) আমাজন (D) কলোরাডো
উত্তর : (C) আমাজন।
(২০৬৮) গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্ অনুসারে, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদী (World’s Shortest River) হল —
(A) রো নদী (B) ডি নদী
(C) ওব নদী (D) লেনা নদী
উত্তর : (A) রো নদী।
(২০৬৯) পৃথিবীর গভীরতম নদী (World’s Deepest River) হল —
(A) টেমস (B) মিসিসিপি
(C) ইয়াংসি (D) কঙ্গো
উত্তর : (D) কঙ্গো।
(২০৭০) এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of Asia) হল —
(A) ইয়াংসি (B) ব্রহ্মপুত্র
(C) মেকং (D) টাইগ্রিস
উত্তর : (A) ইয়াংসি।
(২০৭১) আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of Africa) হল —
(A) কঙ্গো (B) নাইজার
(C) জাম্বেসি (D) নীল
উত্তর : (D) নীল।
(২০৭২) ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of Europe) হল —
(A) রাইন (B) ভলগা
(C) দানিয়ুব (D) নিপার
উত্তর : (B) ভলগা।
(২০৭৩) উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of North America) হল —
(A) কলোরাডো (B) কলম্বিয়া
(C) মিসিসিপি (D) টেনেসি
উত্তর : (C) মিসিসিপি।
(২০৭৪) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of South America) হল —
(A) ম্যাগডালেনা (B) আমাজন
(C) অরিনোকো (D) পারানা
উত্তর : (B) আমাজন।
(২০৭৫) ওশিয়ানিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of Oceania) হল —
(A) লাচলান (B) কিকোরি
(C) মারে (D) ওয়াইটাকি
উত্তর : (C) মারে।
(WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-42)
(২০৭৬) আন্টার্কটিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (Longest River of Antarctica) হল —
(A) প্রিসকু (B) অনিক্স
(C) সারকো (D) লসন
উত্তর : (B) অনিক্স।
(২০৭৭) ভারতের দীর্ঘতম নদী (Longest River of India) হল —
(A) গঙ্গা (B) যমুনা
(C) সিন্ধু (D) নর্মদা
উত্তর : (A) গঙ্গা।
(২০৭৮) জলপ্রবাহ অনুসারে, ভারতের বৃহত্তম নদী (Largest River of India) হল —
(A) গঙ্গা (B) ব্রহ্মপুত্র
(C) গোদাবরী (D) সিন্ধু
উত্তর : (B) ব্রহ্মপুত্র।
(২০৭৯) ভারতের গভীরতম নদী (Deepest River of India) হল —
(A) গোদাবরী (B) চম্বল
(C) ব্রহ্মপুত্র (D) কাবেরী
উত্তর : (C) ব্রহ্মপুত্র।
(২০৮০) ভূপৃষ্ঠে বহির্জাত প্রক্রিয়ার সর্বাধিক ক্রিয়াশীল মাধ্যম হল —
(A) নদী (B) হিমবাহ
(C) বায়ুপ্রবাহ (D) সমুদ্রতরঙ্গ
উত্তর : (A) নদী।
(২০৮১) পৃথিবীর মোট জলের যে শতাংশ নদনদীতে রয়েছে, তা হল —
(A) ১.০০০% (B) ০.০০০১৫%
(C) ৩০.১০০% (D) ০.০০৬%
উত্তর : (B) ০.০০০১৫%।
(২০৮২) পৃথিবীর মোট স্বাদুজলের যে শতাংশ নদনদীতে রয়েছে, তা হল —
(A) ১.০০০% (B) ২.০৫০%
(C) ৩০.১০০% (D) ০.০০৬১%
উত্তর : (ঘ) ০.০০৬১%।
(২০৮৩) যে বহির্জাত শক্তি ভূমিরূপ পরিবর্তনে সর্বাধিক ভূমিকা নেয় —
(A) নদী (B) হিমবাহ
(C) বায়ুপ্রবাহ (D) সমুদ্রতরঙ্গ
উত্তর : (A) নদী।
(২০৮৪) নদীর ক্ষয়কাজের শেষ সীমা হল —
(A) পর্বত (B) মালভূমি
(C) সমভূমি (D) সমুদ্রপৃষ্ঠ
উত্তর : (D) সমুদ্রপৃষ্ঠ।
(২০৮৫) পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা (World’s Largest River Basin) হল —
(A) কঙ্গো অববাহিকা (B) আমাজন অববাহিকা
(C) ভলগা অববাহিকা (D) ইয়াংসি অববাহিকা
উত্তর : (B) আমাজন অববাহিকা।
(২০৮৬) ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকা (Largest River Basin of India) হল —
(A) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (B) গোদাবরী অববাহিকা
(C) গঙ্গা অববাহিকা (D) মহানদী অববাহিকা
উত্তর : (C) গঙ্গা অববাহিকা।
(২০৮৭) নদীর উৎস অঞ্চলের জল সংগ্রহের ক্ষেত্রকে বলে —
(A) নদী অববাহিকা (B) ধারণ অববাহিকা
(C) জলবিভাজিকা (D) নদী উপত্যকা
উত্তর : (B) ধারণ অববাহিকা।
(২০৮৮) যে খাত বরাবর নদীর জল প্রবাহিত হয়, তাকে বলে —
(A) নদী উপত্যকা (B) জলবিভাজিকা
(C) ধারণ অববাহিকা (D) নদীমঞ্চ
উত্তর : (A) নদী উপত্যকা।
(২০৮৯) প্রধান নদী, উপনদী, প্র-উপনদী, শাখানদী ও প্র-শাখানদী দ্বারা সৃষ্ট নিষ্কাশন অঞ্চলকে —
(A) নদী উপত্যকা (B) জলবিভাজিকা
(C) নদী অববাহিকা (D) ধারণ অববাহিকা
উত্তর : (C) নদী অববাহিকা।
(২০৯০) যে উচ্চভূমি দুটি নদী অববাহিকাকে পৃথক করে, তাকে বলে —
(A) নদী উপত্যকা (B) ধারণ অববাহিকা
(C) নদী অধিত্যকা (D) জলবিভাজিকা
উত্তর : (D) জলবিভাজিকা।
(২০৯১) পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিভাজিকা (World’s Largest Water Divide) হল —
(A) মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমি (B) হিমালয় পর্বতমালা
(C) আল্পস পর্বতমালা (D) হিন্দুকুশ পর্বতমালা
উত্তর : (A) মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমি।
(২০৯২) ভারতের বৃহত্তম জলবিভাজিকা (Largest Water Divide of India) হল —
(A) পশ্চিমঘাট পর্বত (B) হিমালয় পর্বত
(C) পূর্বঘাট পর্বত (D) বিন্ধ্য পর্বত
উত্তর : (D) বিন্ধ্য পর্বত।
(২০৯৩) নদীর উচ্চগতিতে প্রধান কাজ হল —
(A) নিম্নক্ষয় (B) বহন
(C) পার্শ্বক্ষয় (D) সঞ্চয়
উত্তর : (A) নিম্নক্ষয়।
(২০৯৪) নদীর মধ্যগতিতে প্রধান কাজ হল —
(A) পার্শ্বক্ষয় (B) বহন
(C) সঞ্চয় (D) A ও B উভয়ই
উত্তর : (D) A ও B উভয়ই।
(২০৯৫) নদীর নিম্নগতিতে প্রধান কাজ হল —
(A) নিম্নক্ষয় (B) পার্শ্বক্ষয়
(C) বহন (D) সঞ্চয়
উত্তর : (D) সঞ্চয়।
(২০৯৬) যে প্রকার ক্ষয়কাজে নদীতে প্রবহমান জলের আঘাতে নদীখাত ও নদীপার্শ্ব ক্ষয় হয়, তা হল —
(A) জলপ্রবাহ ক্ষয় (B) ঘর্ষণ ক্ষয়
(C) অবঘর্ষ ক্ষয় (D) বুদবুদ ক্ষয়
উত্তর : (A) জলপ্রবাহ ক্ষয়।
(২০৯৭) যে প্রকার ক্ষয়কাজ নদীগর্ভের শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ করে, তা হল —
(A) জলপ্রবাহ ক্ষয় (B) বুদবুদ ক্ষয়
(C) অবঘর্ষ ক্ষয় (D) ঘর্ষণ ক্ষয়
উত্তর : (B) বুদবুদ ক্ষয়।
(২০৯৮) যে প্রকার ক্ষয়কাজে নদীবাহিত শিলাখন্ড নদী তলদেশে গর্ত সৃষ্টি করে, তা হল —
(A) বুদবুদ ক্ষয় (B) ঘর্ষণ ক্ষয়
(C) অবঘর্ষ ক্ষয় (D) দ্রবণ ক্ষয়
উত্তর : (C) অবঘর্ষ ক্ষয়।
(২০৯৯) যে প্রকার ক্ষয়কাজে জিপসাম, চুনাপাথর নদীর জলে দ্রবীভূত হয়, তা হল —
(A) অবঘর্ষ ক্ষয় (B) দ্রবণ ক্ষয়
(C) বুদবুদ ক্ষয় (D) ঘর্ষণ ক্ষয়
উত্তর : (B) দ্রবণ ক্ষয়।
(২১০০) যে প্রকার ক্ষয়কাজের ফলে বর্ষাকালে নদীর পাড় ধ্বসে যায়, তা হল —
(A) বুদবুদ ক্ষয় (B) অবঘর্ষ ক্ষয়
(C) জলপ্রবাহ ক্ষয় (D) ঘর্ষণ ক্ষয়
উত্তর : (C) জলপ্রবাহ ক্ষয়।
(WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-42)

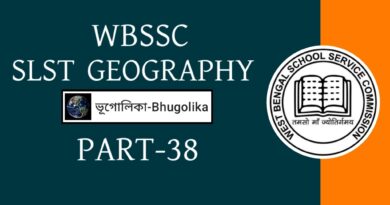
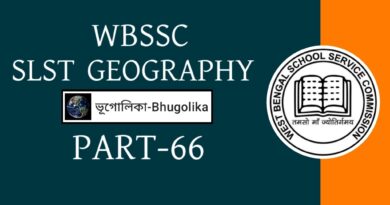

Pingback: WBSSC SLST GEOGRAPHY PART-43 - ভূগোলিকা-Bhugolika