Topic – Fish of Sundarban
প্রসঙ্গ – সুন্দরবনের মাছ
ভূগোলিকা-Bhugolika -এর ‘ভৌগোলিক প্রবন্ধ’ বিভাগে আপনাকে স্বাগত জানাই। ভৌগোলিক প্রবন্ধে আমরা ভূগোলের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিস্তারিত তথ্য পেয়ে থাকি, যা আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক হয়। আজকের ভৌগোলিক প্রবন্ধ : Topic – Fish of Sundarban । আশাকরি, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আপনি সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাবেন।

সুন্দরবন, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ভারত ও বাংলাদেশের অন্তর্গত ১০,২৭৭ বর্গকিমি আয়তনের এই বাদাবনে ‘জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ’। পাশাপাশি, সুন্দরবন সৃষ্টির শুরু থেকে মৎস্যসম্পদের একটি বড় আধার হিসেবে চিহ্নিত। নদী-খাঁড়ি ও খাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনের ১৮৭৪ বর্গকিমি (৩১.১৪%) এবং ভারতের সুন্দরবনের ১৭০০ বর্গকিমি (৩৯.৯০%) এলাকা জলধারার অন্তর্গত। সুন্দরবনের নদ-নদী, খাল-খাঁড়ি ও মোহনাগুলি মৎস্যসম্পদের ভান্ডার। মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য প্রজাতি সুন্দরবনের সার্বিক জীববৈচিত্র্যেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুন্দরবনে প্রতিদিন দু’বার জোয়ার-ভাটা হয়। সমুদ্র থেকে আগত জোয়ারের জল সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীকে স্বাভাবিকভাবেই লবণাক্ত সহিষ্ণু করে তুলেছে। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নদীসমূহের পলি, খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ স্বাদু জল মোহনাঞ্চলের নোনা জলের সঙ্গে মিশে যায়। বনের লতাপাতাও জলকে সমৃদ্ধ করে। ফলে জৈব-অজৈব পুষ্টি যেমন জলের উর্বরতাকে বৃদ্ধি করে, তেমনই মাছের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। (Topic – Fish of Sundarban)
সুন্দরবন নানা ধরনের পেশাজীবীদের জীবিকার উৎস, তারই একটি অংশ মৎস্যজীবী। তারা সুন্দরবনের অসংখ্য ছোটোবড়ো নদী-খালে বংশ পরম্পরায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে চলে যান সুন্দরবনের ভেতরে। দিন-রাত বৈঠা বেয়ে লোকালয় থেকে তারা পৌঁছান বনের গভীরে। যারা সুন্দরবনে মাছ ধরেন, তাঁরা দিন-রাতের হিসেব করে চলেন না। সুন্দরবনে ‘গোন’ (Gon) হিসেব করে মাছ ধরা চলে। গোন দুই প্রকার — ভরা গোন অর্থাৎ ভরা কটাল (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে) এবং মরা গোন অর্থাৎ মরা কটাল (কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে)। সাধারণত ভাটার সময় মাছ ধরতে ব্যস্ত থাকেন জেলেরা, জোয়ারের সময় তারা রান্না-বান্না করেন, বিশ্রাম নেন। সুন্দরবনের জেলেরা সবচেয়ে বেশি মাছ ধরেন ‘চরগড়া’ (Chargora) বা ‘চরপাটা’ (Charpata) জাল দিয়ে, যা আবার ‘গোপ জাল’ (Gop Jaal) নামেও পরিচিত। খালের চরে ভাটার সময় এই জাল পেতে রাখা হয়। খাল জোয়ারের জলে ডুবে গেলে সেখানে যেসব মাছ আটকে যায়, সেগুলো পরে ভাটার সময় জেলেরা সংগ্রহ করেন। সুন্দরবনে মাছ ধরার আরেকটি প্রধান পদ্ধতি হল ‘ভাসান জাল’ (Bhasan Jaal)। অপেক্ষাকৃত বড়ো নদীতে মাছ ধরতে আড়াআড়ি বিশাল আকৃতির এই জাল পাতা হয়। এছাড়া সুন্দরবনে ইলিশ জাল, কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, ফাঁদ জাল, বেড় জাল, ঠেলা জাল, রকেট জাল প্রভৃতি নানা ধরনের জাল ব্যবহার করে মাছ ধরা হয়।
সুন্দরবনের নদী-খালে অনেকে ডিঙি-নৌকাতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরেন। মাছ ধরার বড়শি ‘দাওন’ নামেও পরিচিত। লম্বা সুতায় অনেকগুলো বড়শি গেঁথে দাওন তৈরি করা হয়। এক দাওনে শতাধিক বড়শি থাকতে পারে। দুইভাবে দাওন পাতা হয় — (১) ডোবা দাওন : এই দাওনের বড়শিগুলো জলের একদম নিচে ডুবে থাকে। এই বড়শিতে আধার হিসেবে দেওয়া হয় ছোট কাঁকড়া। ডোবা দাওনে কাইন, মেদ ইত্যাদি মাছ। (২) ভাসা দাওন : এই দাওন জঙ্গলের পাশ দিয়ে, গাছের ভেতর ও শিকড়ের ভেতর পাতা হয়। এই দাওনে আধার হিসেবে দেওয়া হয় চিংড়ি। ভাসা দাওনে পাতাড়ি (ছোটো ভেটকি), জাভা ইত্যাদি মাছ। যেসব জেলেরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরেন, তাঁরা ‘বৈশেল’ (Boishel) নামে পরিচিত। বৈশেল জেলেরা মূলত মরা গোন অর্থাৎ মরা কটালে মাছ ধরে থাকেন। সুন্দরবনে বাঁশের তৈরি এক ধরনের খাঁচা জলেতে ডুবিয়ে মাছ জিইয়ে রাখা হয়। ওই বাঁশের খাঁচা ‘হাপর’ (Hapor) নামে পরিচিত।
ভৌগোলিক প্রবন্ধ : উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকনৃত্য
ভারতের অন্তর্গত সুন্দরবনে ১৭২ প্রজাতির মাছ এবং ২০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (সূত্র : ইন্ডিয়া ক্লাইমেট ডায়লগ)। আর বাংলাদেশের সুন্দরবনে ১৯৬ প্রজাতির মাছ এবং ২০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (FAO Survey ২০০১)। সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এক, সাদা মাছ অর্থাৎ চিংড়ি ব্যতীত সমস্ত মাছ এবং দুই, চিংড়ি — মূলত বাগদা-গলদা চিংড়ি (Lobster & Prawn) এবং অন্যান্য (চাকা চিংড়ি/সাদা চিংড়ি, হরিণা চিংড়ি, ফুল চিংড়ি, গোদা চিংড়ি ইত্যাদি)। সুন্দরবনে একই মাছের বিভিন্ন স্থানীয় নাম রয়েছে। যেমন — চিত্রা (Chitra), পায়রাতালি (Paira), বিশতারা (Bishtara), বোথরা (Bothra) একই মাছ ; কাইক্কা (Kaikka), কাকিলা (Kakila), কাইকশেল (Kaikshel) একই মাছ ; রামচোষ (Ramchos) ও তোপসে/তপসে (Topshe) একই মাছ। সুন্দরবন তথা পৃথিবীর সকল ক্রান্তীয় ম্যানগ্রোভ বনের প্রতীক মাছ হল মেনো/মেনি (Meno/Meni) মাছ, যা আবার ডাহুক (Dahook) মাছ নামেও পরিচিত। খুবই ছোটো আকারের এই মাছের ইংরেজি নাম মাডস্কিপার (Mudskipper)। এছাড়া আকার অনুসারেও মাছের নামবদল হয়। যেমন : ছোটো ভেটকি মাছ ‘পাতাড়ি’ (Patari), মাঝারি ভেটকি মাছ ‘ভেটকি’ (Bhetki), বড়ো ভেটকি মাছ ‘কোরাল’ (Coral) নামে পরিচিত। সুন্দরবনের নদী-খালে জেলেদের জালে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে গলদা, বাগদা, ইলিশ, কাইন মাগুর, টেকচাঁদা, রূপচাঁদা, দাতিনা, ট্যাংরা, তপসে, পোয়া, ভেটকি, পারশে, বাটা, তাড়িয়াল, ভোলা, লইট্টা, পানপাতা প্রভৃতি মাছ। এছাড়াও সুন্দরবনের নদী-খালে বেশকিছু বিরল ও দামী প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। যেমন — (১) সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো মাছ হল কই ভোলা (Koi Bhola) মাছ। এই মাছ আকৃতিতে বিশাল হয়, ৫০ থেকে ৭০ কেজি ওজনেরও হয়ে থাকে। তবে এই মাছ সচরাচর দেখা যায়না। সুন্দরবনের গ্রামীণ ভাষায় কই ভোলা মাছকে ‘জংলি মাছ’ (Wild Fish) বলা হয়। এই মাছ ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। (২) জাভা (Java) মাছ, আন্তর্জাতিক বাজারে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা। কারণ এই মাছের ‘পটকা’ দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়। প্রতি কেজি জাভা মাছ তিন-চার হাজার থেকে ১১ হাজার টাকাতে বিক্রি হয়। ১০০ গ্রাম পটকার দাম ওঠে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা! (৩) তেলিয়া ভোলা (Telia Bhola) মাছ, যা ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত, এই মাছ স্ত্রী, পুরুষ ছাড়াও উভয় লিঙ্গেরও হয়ে থাকে। উভয় লিঙ্গের তেলিয়া ভোলার স্থানীয় নাম খচ্চর ভোলা। (৪) সুন্দরবনের একটি বিশেষ মাছ হল গনগনে (Gongone) মাছ। জীবিত অবস্থায় এই মাছ হাত দিয়ে ধরলে অল্প শব্দে ব্যাঙের মতো গনর গনর করে। তাই এই সুস্বাদু মাছের নাম গনগনে। অনেক সময় সন্তান জন্মের পর মায়ের মাতৃদুগ্ধের অভাব দেখা যায়। এই মাছ খেলে মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই একে অনেকে ‘দুধ-মাছ’ (Milk Fish) বলে থাকেন।
সুন্দরবনের নদীতে নানা জাতের মাছ রয়েছে। আর মাছের নামেই সুন্দরবনের অনেক স্থানের নামকরণ হয়েছে। পারশেখালি, কৈখালি, দাঁতিনাখালি, ভেটকিখালি প্রভৃতি স্থানগুলির নাম মাছের নামেই গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের নদীতে একেক মাছের আবাসস্থল একেক জায়গায়। নদীর ওপরের দিকে থাকে ট্যাংরা মাছ। পায়রা, কাইন ও ভেটকি মাছ থাকে মাঝবরাবর। আর নিচের দিকে গভীর জলে থাকে মেদ মাছ। দাঁতিনা, পারশে ও চিংড়ি মাছ থাকে চরের কাছাকাছি। সব মাছের প্রজননকাল আবার একই সময়ে নয়। বাদাবনে নদীর তীরবর্তী অংশে ধানি ঘাস, হেতাল, হরগোজা ও গোলপাতা জন্মে। গোলপাতার বনে মাছেদের ঝাঁক বেশি দেখা যায়। বিশেষত পায়রা, পারশে, ভাঙ্গান, গলদা চিংড়ি মাছ। এছাড়া সুন্দরবনে রয়েছে মিষ্টিজলের বিল বা জলাভূমি, যেখানে স্বাদুজলের মাছ পাওয়া যায়। যার অধিকাংশই জিওল মাছ, যেমন কই, শিঙ্গি, মাগুর, টাকি, শোল ইত্যাদি। (Topic – Fish of Sundarban)
ভৌগোলিক প্রবন্ধ : মুর্শিদাবাদের আহিরণ বিল
সুন্দরবনের নদী-খাল থেকে মাছ ধরা নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে। ভারতের সুন্দরবনে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ‘কোর এরিয়া’-তে সকল প্রকার মানবিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। তবে সরকারি অনুমতি (BLCs) সাপেক্ষে মানবচালিত নৌকার সাহায্যে ‘বাফার এরিয়া’-তে মাছ ধরা যায়। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ইলিশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বরের পূর্ণিমার ৫ দিন আগে থেকে অক্টোবরের পূর্ণিমার ৫ দিন পর পর্যন্ত সুন্দরবনের ঠাকুরানি, মাতলা ও রায়মঙ্গল নদী অববাহিকার ৫ বর্গকিমি এলাকাতে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে সাম্প্রতিকালে গবেষকদের একটি দল সরকারের কাছে সুন্দরবনে মাছ শিকারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করে দেওয়া এবং প্রজনন ঋতুতে মাছ শিকার বন্ধের অনুরোধ করেছেন। বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনে অভয়ারণ্য ঘোষিত অঞ্চলের ৩০টি খাল এবং ২৫ ফুটের কম প্রশস্ত খালে সারা বছরই মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এছাড়া প্রজনন মরসুমের কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ বনবিভাগ প্রতি বছর ১ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনের সকল নদী ও খালে মাছ ধরা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনেও পড়ছে। আর তার প্রভাব মাছ সহ সমগ্র সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ওপরই লক্ষ্যণীয়। রয়েছে বিভিন্ন প্রকার দূষণ। সুন্দরবনের জলীয় বাস্তুসংস্থানে বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের অনেক প্রজাতির মাছ বর্তমানে অস্তিত্বের সংকটে। চন্দনা ইলিশ, লাক্ষা, কাজলি, লাল চেউয়া, লাল দাঁতিনা, দাগি কান মাগুর প্রভৃতি মাছ ক্রমশ বিরল হচ্ছে। আর একশ্রেণীর লোভী মানুষ সুন্দরবনের নদী-খালে বিষ/কীটনাশক দিয়ে মাছ শিকার করার ফলে, সমগ্র জলজ বাস্তুতন্ত্রই আজ বিপদে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবনের সমগ্র জীববৈচিত্র্যও। উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা না নিলে, সুন্দরবনের বিপুল মৎস্যবৈচিত্র্য ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। (Topic – Fish of Sundarban)
উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল নির্যাস [XI : Semester-II]
লেখকঃ- অরিজিৎ সিংহ মহাপাত্র (পার্শ্বলা, বাঁকুড়া)
তথ্যসূত্রঃ- কালের কন্ঠ ; প্রথম আলো ; আনন্দবাজার পত্রিকা ; নিউজ ১৮ বাংলা ; Wikipedia ; India Climate Dialogue ; কৃষি ও আমিষ সাপ্তাহিক পত্রিকা (বাংলাদেশ) ; Barcik News Portal ; পরিবেশ নীতি বনাম সুন্দরবনের মৎসশিকারিরা – অভিজিৎ মিস্ত্রি ও নাসরিন বানু – লোকজীবন চর্চা
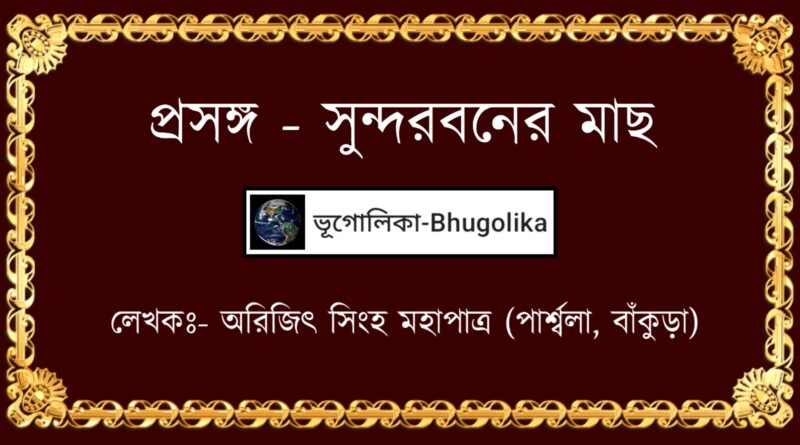
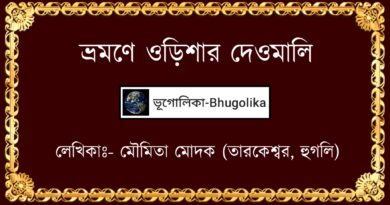
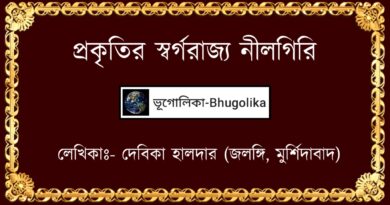
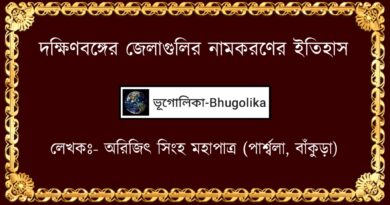
Pingback: Declining Sundarban Over Time - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Dampier-Hodges Line of Sundarban - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Spatial Distribution of Vegetation in Sundarban - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Sundarban & Life - Livelihoods - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Five-Year Plans of India - ভূগোলিকা-Bhugolika
Outstanding
Pingback: Topic - Will-o'-the-Wisp - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Tourism - Biharinath Hill of Bankura - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: WBPSC ASSISTANT MASTER/MISTRESS GEOGRAPHY SYLLABUS - ভূগোলিকা-Bhugolika
Pingback: Fourth Industrial Revolution - ভূগোলিকা-Bhugolika